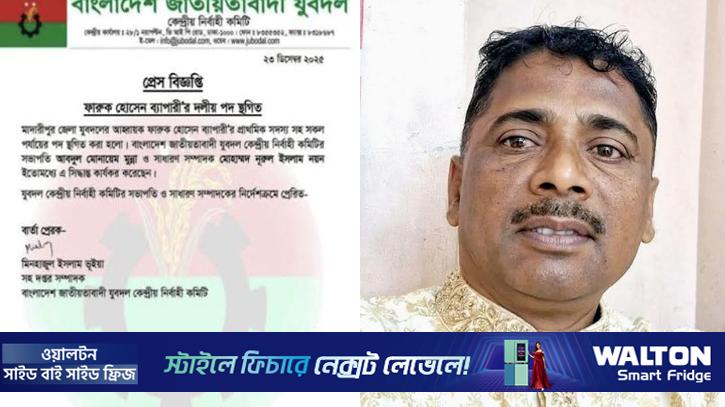বুকার প্রাইজ ২০২৫ এর সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পাওয়া ‘দ্য লনলিনেস অব সোনিয়া অ্যান্ড সানি’ উপন্যাসের লেখক কিরণ দেশাইয়ের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে বুকার কর্তৃপক্ষ। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃত্তিকা তৃণ।
প্রশ্ন: আমার বইটির পেছনের অনুপ্রেরণা
উত্তর: এমন একটি গল্প লিখতে চেয়েছিলাম যেখানে আধুনিক বিশ্বের ভালোবাসা ও নিঃসঙ্গতার কথা থাকবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এমন এক ধরনের রোমান্স সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, যেখানে পুরোনো দিনের সৌন্দর্য আভাস থাকবে। বাবা-মায়ের সময়ে, বিশেষ করে আমার দাদা-দাদীর সময়ে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম এবং প্রায়ই একটি স্থানকেন্দ্রিক ভারতীয় প্রেমের গল্প লেখা হতো। কিন্তু আজকের যুগে কোনো প্রেমের গল্পের পথচলা স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক ও ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
আমার চরিত্ররা ভাবে: কেন এই মানুষটি? কেন আর কেউ নয়? কেন এই স্থান, অন্য কোথাও নয়? অতীতে মানুষ যেখানে থাকার কথা ছিল, সবসময় সেই জায়গা জুড়েই থাকত।
আমার অনিশ্চিত প্রেমিকযুগল সোনিয়া ও সানি ইউরোপ, ভারত এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানজুড়ে মিলিত হয়, বিচ্ছিন্ন হয়; নিজেদের পরিচয় তারা ক্রমেই আরও তরল ও পরিবর্তনশীল রূপে আবিষ্কার করে।
যখন আমি ভূগোল ও প্রজন্ম পেরিয়ে লিখতে শুরু করে বুঝতে পারি, আমার উপন্যাসের পরিধি আরও বিস্তৃত করা সম্ভব। শুধু রোমান্টিক নিঃসঙ্গতার গল্প নয়, বরং এক বৃহত্তর অর্থে নিঃসঙ্গতার গল্প লিখতে পারি। যেখানে শ্রেণি ও বর্ণের বিভাজন, জাতির মধ্যে অবিশ্বাস এবং দ্রুত বিলীন হতে থাকা অতীতের পৃথিবী সবই যেন একেকটি নিঃসঙ্গতার রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
প্রশ্ন: যে বইটি আমাকে পড়ার প্রেমে ফেলেছিল
উত্তর: কেনেথ গ্রাহামের উপন্যাস ‘দ্যা উইন্ড ইন দ্যা উইলোজ’। আমার শৈশব ছিল একেবারে ভারতীয়। বুকশেলফ ভরতি ইংরেজি শিশুসাহিত্যের বই ছিলো। কিছু আবার আমার বাবা-মায়ের সময়কার, যেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। আমার কাছে থাকা কেনেথ গ্রাহামের বইটি ১৯৫৪ সালের কাপড়ের মলাটে বাঁধা সংস্করণ। পাতাগুলো এখন ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু ছবিগুলো এখনো উজ্জ্বল ও জীবন্ত। কোন পথে যাবে মানুষ? নিরাপদ আশ্রয়ে, নাকি অজানার পথে? এই গল্পটি আমাকে প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার বিষয়টি শিখিয়েছিল। যখনই ভাবি “Toad of Toad Hall” তার গাড়ির হর্ন ‘poop poop!’ করছে, কিংবা মোল “A mole! mole!” বলে যুদ্ধের ডাক দিয়ে দুষ্ট উইজেলদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, হেসে ফেলি জোরে জোরে।
প্রশ্ন: যে বইটি আমাকে লেখক হতে প্রেরণা দিয়েছিল
উত্তর: কালভিনো এমন একজন লেখক যিনি শিশুদের খেলাধুলা ও কল্পনা জগতের স্বাদ প্রাপ্তবয়স্কদের সাহিত্যেও অনায়াসে নিয়ে আসেন। বিশ বছর বয়সে যখন আমার প্রথম উপন্যাস লেখছিলাম তখন আর্চিবল্ড কোলকুহনের অনুবাদে তার দ্যা বেরেন ইন দ্যা ট্রি বইটি মাথায় ঘুরপাক করতো।
নায়ক কজিমোকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সে একদিন শামুক খাওয়া নিয়ে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে রেগে বাড়ি ছেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তার অনুপ্রেরণায় আমি এক ভারতীয় ছেলেকে নিয়ে লিখেছিলাম। সে গাছের ওপরেই নিজের জগৎ বানিয়ে নেয়। অনেক বছর পর এসে এখন কালভিনোর ‘সিক্স মেমোস ফর দ্য নেক্সট মিলেনিয়াম’ পড়েছি। এক অসাধারণ রচনা। তিনি নান্দনিকতার এক নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন: লাইটনেস, দ্রুততা, বহুমাত্রিকতা, দৃশ্যমানতা।
শেষ মেমোটি লেখার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এর নাম হওয়ার কথা ছিল Consistency—যেখানে হয়ত নানা চিত্র, ধারণা ও কল্পনার প্রাচুর্যের নিহিত ঐক্যকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ছিল। আমি বিস্মিত হয়ে দেখছিলাম, এই নীতিগুলোর সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের, বিশেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তার অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই ধারণাগুলোর ফলাফল কী হতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা, শিল্প সাংস্কৃতিক, কিংবা আধ্যাত্মিক স্তরে এসব নিয়ে ভাবতে থাকি।
প্রশ্ন: যে বইটি আমার পৃথিবী দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিল
উত্তর: সালমান রুশদি একবার বলেছিলেন, তিনি The Moor’s Last Sigh লিখেছিলেন এক ধরনের বিরক্তি থেকে জন্ম নেওয়া প্রেরণায়। বিরক্তি কারণ ছিলো, সংখ্যালঘুরা নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় “কম ভারতীয়” এমন একটি কথা কথা শুনে। এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভারতের দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কোচিনের কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদি এবং পর্তুগিজ ক্যাথলিকদেরকে।
উপন্যাসে যখন অরোরা দা গামা ও আব্রাহাম জোগোইবি একে অপরের সঙ্গে দেখা করে ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, রুশদি সেই মিলনকে এক অনুপম গদ্যে বর্ণনা করেছেন। তাদের সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া এক নতুন পরিচয়কে রুশদির নিজের ভাষায় বলা যায় “a minority of one: Moraes Zogoiby.”এই উপন্যাসটি পড়ে উপলব্ধি করি যে একজন নাগরিক ও একজন লেখকের জীবনের আসল দায়বদ্ধতা সেই “একজনের সংখ্যালঘু”-এর প্রতিই, সেই একক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই, যা সমগ্র পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়।
আমরা যখন মানবাধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার, কিংবা এক ধর্মনিরপেক্ষ জাতির জন্য লড়ি, তখন আমরা আসলে একটি সাহিত্যিক পরিসরকেও রক্ষা করছি একটি এমন স্থানে যেখানে লেখক অন্য পৃথিবী থেকে আসা মানুষদের সম্পর্কে আন্তরিকতা ও গভীর জ্ঞান ভরে লিখতে পারেন।
দা গামা ও জোগোইবি পরিবারদের সম্পর্কে পড়তে পড়তে গভীর পরিচয়ের অনুভূতি পেয়েছিলাম, হৃদয়ের ভেতর এক ধরনের স্নেহের বিকাশ ঘটেছিল।
তখন বুঝেছিলাম—হ্যাঁ, এরা সত্যিই ভারতীয়, ভারতীয় ইহুদি ও ভারতীয় ক্যাথলিক। তাদের জন্ম অন্য কোথাও সম্ভবই নয়।
প্রশ্ন: যে বইটি আমার উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা পালটে দিয়েছিল
উত্তর: নাতাশা উইমারের স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ করা রবের্তো বোলানিয়োর ‘The Savage Detectives’ পড়ে নিশ্বাস আটকে গিয়েছিল আমার। অচেনা কবিদের সীমান্ত অতিক্রম করে ঘুরে বেড়ানোর এই আধুনিক মহাকাব্য আমাকে একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা পুরো পৃথিবীজুড়ে তারা যে অসংখ্য চরিত্রের সঙ্গে মিশে যায়, তাদের মধ্যে বাস করে, তা যেন এক বিক্ষিপ্ত কিন্তু জীবনের সজীব ক্যানভাস।
উপন্যাসটির গঠন যেন এক ধরনের উন্মাদ স্বাধীনতা বহন করে। সংলাপে আছে কথ্য রসের তেজ এবং এর দার্শনিক ভাবনাগুলো এমন একধরনে গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয় যা কখনও কখনও অদ্ভুত মুগ্ধতায় পৌঁছে যায়।
বোলানিয়ো যেন এক অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করেছেন। উপন্যাসটিকে সাধারণত “উপন্যাস” শব্দটির বিপরীত বলে মনে হয়। তা গল্পকে কেন্দ্র করে না বরং গল্পটিকেই ভেঙে দেয় অসংখ্য চলমান অণুতে। এটি কোনো স্থানে বাধা নয়, বরং উপন্যাসকে করে তোলে ‘গৃহহীন’। তবু প্রতিটি বিবরণ নিখুঁত, সূক্ষ্ম। দ্রুতগতিতে চলে, বহু দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় গল্পগুলো, তবু সবগুলোর নিচে এক অদৃশ্য ঐক্য বিরাজ করে— অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, চলমানতা, নামহীনতা, এবং পতাকার অপ্রয়োজনীয়তার মতো বহিমাত্রিক থিমে। যা আজকের পৃথিবীতেও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।
প্রশ্ন: কখন কোথায় আমি সবচেয়ে ভালো লিখি
উত্তর: আমার প্রিয় স্থানগুলো হলো বারান্দা এবং রান্নাঘর। বারান্দায় বর্ষা ও গরমের দিনে লিখতাম, মশা মেরে হানা দিতাম, কখনও কখনও কুকুরদেরও ধাওয়া করতে হতো। আমার নিউ ইয়র্ক সিটির বাড়িতে আমার রান্নাঘরে বসে লিখি। এতে লেখার সঙ্গে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার সংযোগ অনুভূত হয়। কেটলি ফুটছে, লেটুস ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে। শব্দগুলো যেন নিজে থেকেই এগিয়ে চলেছে।

 Sangbad365 Admin
Sangbad365 Admin